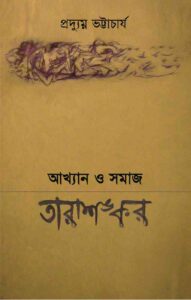
‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় : আদি (1928-38), মধ্য (1939-47) আর অন্ত্য (1948-71)। মধ্য পর্বই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল। রাজনৈতিক ইতিহাসে পাঁজি অনুযায়ী, তারাশঙ্করের এই মধ্য পর্যায়ের শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের কাল থেকে, আর শেষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জনের সালে। এই নয় বছরে তাঁর দশখানি উপন্যাস গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়- ‘ধাত্রী দেবতা’ (1939), ‘কালিন্দী (1940), ‘কবি’ (1942), গণদেবতা (1942), ‘মন্বন্তর’ (1944), ‘পঞ্চগ্রাম’ (1944), ‘সন্দীপন পাঠশালা’ (1945), ‘ঝড় ও ঝরা পাতা’ (1946), ‘অভিযান’ (1947), আর হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (1947)। তাছাড়া এগারোখানি ছোটোগল্পের বই আর পাঁচটা নাটকও বেরোয় এই সময়ের মধ্যে। পূর্বতন পর্বের এগারো বছরে (1928-38), বেরিয়েছিল ছয়টি উপন্যাস আর তিনটি ছোটোগল্পের সংকলন। অতএব নিছক প্রাচুর্যের দিক দিয়ে 1939-47-এর পর্বকে তাঁর সৃষ্টির বসন্ত-পর্যায় বলতে পারি।
পরিমাণের সুত্রে আর একটা প্রসঙ্গ এসে যায়। “বেদেনী” (1939), “পৌষলক্ষ্মী” (1944), “তমসা” (1945) বা “কামধেনু”-র (1946) মতন গল্প লিখলেও, এই দ্বিতীয় পর্বে¸ প্রথম পর্বের তুলনায়, ছোটোগল্পের ফলন অনেক কম : প্রায় অর্ধেক। অন্য পক্ষে, সংখ্যায় তো বটেই, গুণের দিক দিয়েও, এই পর্ব তারাশঙ্করের উপন্যাসের যুগ ; তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি এই বসন্ত-পর্যায়ের ফসল।
অর্থাৎ, যদিও ছোটোগল্পকে বাহন করে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক দিগ্বিজয়ের সুত্রপাত, 1939-এর পর থেকে, ক্রমশ তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে উপন্যাস। কী তার কারণ? বাংলা বইয়ের বাজারের যা হালচাল, তাতে এই বাহন-বদলের একটা সরল আর্থিক ব্যাখ্যার টান প্রায় অরোধ্য। আমাদের সমাজে সাহিত্যও যেহেতু পণ্য, তার কেনাবেচায় বাজারের নিয়ম ত্রিয়াশীল। বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ীদের কাছে ছোটোগল্পের তুলনায় উপন্যাসের কদর এবং চাহিদা বেশি ; সুতরাং ছোটোগল্পের চেয়ে তার দরও বেশি, বাজারও বড়ো। ছোটোগল্পের এই চিরস্থায়ী মন্দা কীভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে তিরিশ দশকের শুরুতে লেখক মহলে কিছু জল্পনা কল্পনাও হয়েছিল। বইপত্রের কাটতি বজায় রাখা বা বাড়ানোর পেছনে যেমন বিজ্ঞাপনের কারসাজি আছে, বাজারের এই টানও তেমন বিজ্ঞাপনে টের পাওয়া যায়। তাই দেখি, 1940 সালের কোনো বহুবিক্রীত শারদীয় সংখ্যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ‘ল্যাবরেটরি’-কেও বিজ্ঞাপিত করা হয় উপন্যাস হিশেবে! এই যখন পরিস্থিতি, যে-লেখকের সাহিত্যই জীবিকা, তাঁর পক্ষে উপার্জনের তাগিদে উপন্যাসের দিকে ঝোঁকা স্বাভাবিক। এই আর্থিক ব্যাখ্যা তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য? ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কালিন্দী, ‘কবি’ বা ‘গণদেবতা’ বাবদ উপার্জন তাঁকে কলকাতায় যুঝতে, দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল ঠিকই; কিন্তু তাঁর লেখায় আর্থিক প্রবর্তনার ছাপ পড়েছে, অনেক পরে, তাঁর জীবনের শেষের দিকে, নিরপত্তার আর সচ্ছলতার সময়ে; তাঁর শেষ পর্যায়ের অনেক ‘উপন্যাস’ আসলে লম্বিত গল্প। লেখার তাড়নায় উপার্জন করাটা দোষের নয়; যা দোষের, তা হচ্ছে, নিছক উপার্জনের তাগিদে লেখা। আর তারাশঙ্করের আত্মস্মৃতির পাঠকমাত্রই জানেন : উপার্জনের আকর্ষণে লেখার সুযোগ, নিজের সংগ্রাম আর অভাবের সময়ে, কত অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি।
কোনও লেখক, তাঁর সৃষ্টির বিশেষ পর্যায়ে, কোন্ শিল্পরূপকে বেছে নেবেন, সেটা, এক হিশেবে, তাঁর ব্যক্তিগত খুশির, আনন্দের ব্যাপার। তারাশঙ্করের মধ্য পর্বের উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি, এই আনন্দ, এই আবিষ্টতা। 1939-47 পর্যায়ের উপন্যাসগুলির স্বরভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে, নিজের একটি বৃহৎ, বর্ধিষ্ণু পাঠকসমাজকে সম্বোধন করে তাদের সঙ্গে প্রসারিত পর্দায় দীর্ঘমাত্রিক আলাপ জমানোর আনন্দ। এই আনন্দ, ভরবেগ জুগিয়েছে লেখন-প্রক্রিয়ার একটানা স্রোতে।
বড়ো পাঠকসমাজের সঙ্গে প্রসারিত আলাপচারির এই আবিষ্ট আকাঙ্ক্ষার পেছনে সেদিনের ইতিহাসের একটা ভূমিকা ছিল, আর ছিল সেই ইতিহাসের সঙ্গে সংবদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা আর ইডিওলজির বিবর্তন-জনিত চাপ। অভিজ্ঞতা আর ইডিওলজি : কথা দুটোকে যদিও পাশাপাশি লিখছি, এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লক্ষ করা দরকার। অক্ষরেখা-দ্রাঘিমার মতো ইডিওলজি চিহ্নিত করে দেয় অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ; অভিজ্ঞতার আলোয় চেনা যায় ইডিওলজির স্বরূপ। ইডিওলজি বিন্যাস, তাৎপর্য, পুরুষার্থ দেয় অভিজ্ঞতাকে; অভিজ্ঞতা ইডিওলজিকে দেয় অন্তঃসার। উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক রসায়নে ইডিওলজি হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে ইডিওলজি। আমার বিশ্বাস ‘ধাত্রীদেবতা’ (1939) প্রকাশের কিছুকাল আগে থেকে বড়ো বিবর্তন শুরু হয় তাঁর অভিজ্ঞতা-ইডিওলজির। 1939-40-এর কিছু আগে থেকে শুরু হয়ে চল্লিশের দশকের প্রথম ছ-সাত বছর ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের গণরূপ ও চেতনাস্তর দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে ছোটো থেকে বড়ো দিগন্তে। চাষীকে প্রত্যক্ষণের কেন্দ্রে স্থাপনের প্রচেষ্টায়, ‘চৈতালি-ঘূর্ণি’ থেকেই যিনি সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন, জনমানসের এই ব্যাপক, প্রচণ্ড আলোড়নের দিন্- গুলিতে তিনি সাধারণ্যের সঙ্গে আরও প্রসারিত, আরও অবিচ্ছিন্ন, সাহিত্যিক-সংযোগ চাইবেন, এ তো স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পর্বের অনেকগুলি উপন্যাসে তারাশঙ্কর তাঁর 1921-31-এর অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে ফিরে ফিরে দেখছেন চল্লিশ-দশকের জাতীয় আন্দোলনের বিবর্ধমান গণভিত্তির বীক্ষণমঞ্চ থেকে। এই পরিবর্তিত পরিপেক্ষিতে তাঁর অভিজ্ঞতাকে আর ছোটো ফ্রেমে নয়, বড়ো বড়ো কাঠামোয় বেঁধে তার মানে নতুনভাবে বুঝাতে চাইছেন। উপমার ভাষায় বলতে পারি, এবার অভিজ্ঞতার ছাঁদকে ফোটাতে চাইছেন ভাস্কর্যের বদলে স্থাপত্যের রীতিতে। অভিজ্ঞতার বিস্তার দাবি করছে আখ্যান-কাঠামোর বিস্তার, যার সংস্থান নেই ছোটোগল্পের শরীরে।
তবে উপন্যাসের শরীরে এই বিস্তার-যোজনের আঙ্গিক দ্বিতীয় পর্বে এসে অনেকটা যেন বদলেছে পূর্বতন পর্বের তুলনায়। 1928-38 পর্বে দেখি, তারাশঙ্কর কখনও ছোটো- গল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাসের চেহারা দিচ্ছেন- যেমন, “শ্মশানের পথে”-র পরিবর্ধিত রূপ ‘চৈতালি-ঘূর্ণি’ আর “স্রোতের কুটো”-র ‘নীলকণ্ঠ’- কখনও-বা দুটো গল্পকে জুড়ে বানাচ্ছেন উপন্যাস- যেমন, “রাইকমল” আর “মালাচন্দন” এই দুই গল্প সংযোজিত করে ‘রাইকমল’। অর্থাৎ, প্রথম পর্বের ছটি উপন্যাসের মধ্যে তিনটি-ই হচ্ছে পরিবর্ধিত ছোটোগল্প। ছোটোগল্প সম্প্রসারিত করে উপন্যাস-রচনার এই আঙ্গিক, দ্বিতীয় পর্বে শুধু একটি ক্ষেত্রে, ‘কবি’-তে, অনুসৃত ; আর ‘কবি’ ঠিক উপন্যাস নয়, নভেলেট। 1939-47 পর্বে লেখা ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কালিন্দী’ আর ‘গণদেবতা’-‘পঞ্চগ্রাম’-এর সঙ্গে যথাক্রমে “সমুদ্রমন্থন”, “ফল্গু” (প্রথম নাম ছিল “মা”) আর “পিতাপুত্র”-এর যোগ আছে। তারাশঙ্কর নিজে “ফল্গু”-কে ‘কালিন্দী’র আর “পিতাপুত্র”-কে ‘গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম’-এর ‘বীজ’ গল্প বলেছেন। কিন্তু এই গল্পগুলিকে উপন্যাস-দুটির বীজ বলা অযৌক্তিক। কারণ বীজের সঙ্গে বৃক্ষের যা সম্পর্ক, তা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত; ‘কালিন্দী’, ‘গণদেবতা’-পঞ্চগ্রাম’ কোনওক্রমেই “ফল্গু”, “পিতাপুত্র”-এর বিবর্ধিত রূপ নয় (আর “সমুদ্রমন্থন”-এর গল্পাংশকে তারাশঙ্কর ‘ধাত্রীদেবতা’-র কাঠামোয় আভাঙা গেঁথে নিয়েছেন, মুল-কাহিনীর বিপ্রতীপ উপাখ্যান হিশেবে)।
বিস্তার-সঞ্চারের এই যে রীতি-বদল, এ-থেকে কতকটা টের পাওয়া যায়, উপন্যাসের আঙ্গিক-চর্চায় 1939-47-এর বছরগুলিতে তিনি কতটা এগিয়েছিলেন। এই হাত পাকাবার প্রক্রিয়ায় তারাশঙ্কর যেন ক্রমশ বুঝে নিয়েছেন, ছোটোগল্পের বিস্তারের সঙ্গে উপন্যাসের বিস্তারের তফাত শুধু পারিমাণিক নয়, গুণগত। আঙ্গিক দখলে আনার এই প্রক্রিয়া আসলে অভিজ্ঞতা-পরিগ্রহণের নামান্তর। কারণ, লৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পিত অভিজ্ঞতার যে-প্রভেদ, সেটাই আঙ্গিক। অর্থাৎ ব্যাপারটা একই প্রক্রিয়ার দুই দিক : এক দিকে আঙ্গিকের বিকাশ ক্রমশ সুচি-চিহ্নিত করেছে তাঁর অভিজ্ঞতাকে; অন্য অভিজ্ঞতার বিকাশ ভাঙাগড়ার মারফত ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত, লক্ষ্যভেদক্ষম করে তুলেছে তার আঙ্গিককে। একই উপন্যাসের একাধিক লেখনের, রূপান্তরের, মধ্যেও ছড়িয়ে আছে এই প্রক্রিয়ার, এই সংঘর্ষের চিহ্ন। ওপরের বর্ণনায় ব্যাপারটা যত নৈর্ব্যক্তিক শোনাচ্ছে, আসলে তা নয়। কারণ, বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াটি ঘটিয়েছেন একজন বিশেষ শিল্পী- তারাশঙ্কর- নিজের মধ্যস্থতায়, শক্তিতে; প্রবল অক্লান্ত একনিষ্ঠ সক্রিয়তায়। এই সক্রিয়তার প্রায় কোনও তুলনা নেই, বাংলা উপন্যাস-লেখার সমস্ত ইতিহাসে। (ক্রমিক পুনর্লেখনের এই রীতিকে উপন্যাসের হয়ে-ওঠার, জৈবিক বিকাশের, প্রক্রিয়া বলে মনে করতেন তারাশঙ্কর। তাঁর অপ্রকাশিত ডায়রির (1944) এক জায়গায় এ-বিষয়ে স্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায়। ‘পঞ্চগ্রাম’ আবার আগাগোড়া নতুন করে লিখেছেন শুনে কোনও সাহিত্যিক বিরূপ মন্তব্য করেন। এতে ক্ষুব্ধ তারাশঙ্কর নিজের ডায়রিতে লেখেন, উপন্যাসের প্রথম-পাঠ সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর সঙ্গে তুলনীয়, তার পরিশুদ্ধ-পাঠের- তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে সংশোধন মানেই বিবর্ধন- সঙ্গে তুলনা চলে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত মানুষের। ‘সৃষ্টিগুলিকে অসমাপ্ত রেখে যে যায়- সে প্রগতিশীল নয়- অসহিজ্ঞু, সার্থকতালোভী স্রষ্টা। তার সৃষ্টি মতো সেও অসম্পূর্ণ। সন্তান প্রসব করেই মায়ের কর্তব্য শেষ হয় না। তাকে সবলাঙ্গ সম্পূর্ণ মানুষ করে দেওয়ার পর- তার মাতৃত্ব সার্থক সম্পূর্ণ হয়।‘)
অভিজ্ঞতার আর আঙ্গিকের এই অন্যোন্য বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর যে-উপন্যাসে আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতি অর্জন করেছেন, তা হচ্ছে, ‘গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম’ (1942-44)। পৃথক বই হিশেবে চললেও, এরা একটা এপিক উপন্যাসের দুটো খণ্ড। তারাশঙ্করের আদি পরিকল্পনাও ছিল তা-ই- ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ আর ‘পঞ্চগ্রাম’ নাম দিয়ে দুই খণ্ডে একটি উপন্যাস লিখবেন, যার নাম হবে ‘গণদেবতা’।
‘আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতি’- এই শব্দদুটি দিয়ে যে-অর্জিত সিদ্ধির কথা বলতে চাইছি, তার মূল উপাদান এইগুলি : ক)’চৈতালি-ঘূর্ণি’ (1931) থেকে প্রায় দীর্ঘ এক যুগ, যে-বিষয়বস্তুকে উপন্যাসের শরীরে তারাশঙ্কর ক্রমাগত বাঁধতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে উঠেছেন এই এপিক উপন্যাসে। খ)বিষয়-বিষয়ীর এই ঐক্যের পাশাপাশি দেখতে পাই, চেতনার আপেক্ষিক স্বচ্ছতা, বিস্তার; চাষীর সঙ্গে সমপ্রাণতা। তাই, ‘গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম’-এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যস্থতায় সঞ্চারিত হতে পেরেছে সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতা; আঞ্চলিক সীমার মধ্যে থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশের বাস্তবতার ছাঁদ। গ)ব্রত-পার্বণ-কথকতার বিন্যাস অন্তর্গ্রথিত করে নিয়ে ‘গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম’-এ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন বাংলা উপন্যাসের নতুন রূপ, দেশজ রূপ, যার কাঠামোর সঙ্গে দেশের তৎকালীন (1921-47) গ্রাম্য সামাজিক কাঠামোর সমরূপতা (homology) লক্ষণীয়। ওপরে, যা লিখিছি তা থেকে অন্তত এ-টুকু, আশা করি, স্পষ্ট যে : উপন্যাসচর্চায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর হয়ে উঠেছেন ‘গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম’-এ(1942-44)। আর, এ-ধরণের প্রতিভাস্বাতন্ত্র্যবান শিল্পকাজের পক্ষে যা স্বাভাবিক : ‘গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম’ বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যেরও কিছু রূপান্তর ঘটিয়েছে- অংশত পালটেছে আমাদের উপন্যাসের সংজ্ঞা, পরিধি, মানদণ্ড। এই সিদ্ধির পেছনে যে-দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাস- আত্মপরিচয় ও আত্মগঠনের দীর্ঘ পটভূমি- সংক্ষেপে তা বলে নিলে তারাশঙ্করকে বোঝা এবং তার সাফল্যের মুল্যায়ন সহজ হবে।‘…
প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, ‘আখ্যান ও সমাজ তারাশঙ্কর’, অবভাস
বইটি সংগ্রহ করার জন্য ক্লিক করুন- https://www.ababhashbooks.com/art-language-literary-studies/akhyan-o-samaj-tarashankar.html


